

লাইভ প্রতিবেদক: মানুষ এক অদ্ভুত প্রাণী! প্রাণীজগতের এই একটি প্রাণীই আছে, যারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে দার্শনিক চিন্তাভাবনা করতে শিখেছে। মনুষ্য প্রজাতির জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ভেবে আসছে মহাবিশ্বে তারা কেন এলো, কোথা থেকে এলো, কোথায়ই বা যাবে, এই প্রশ্নগুলো। লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমাদের প্রজাতির পূর্বসূরীরা সারাদিনের শিকার শেষে ক্লান্ত শরীরে রাতের আকাশে চোখ মেলে অপূর্ব নক্ষত্র আর ছায়াপথের ছায়া দেখে বিস্মিত হতো।
আর তাদের মনে এই প্রশ্নগুলো ঘুরে ঘুরে মরতো। স্থলচর এইসব হোমো স্যাপিয়েন্স পানিতে চলতে শিখেছে, আকাশেও উড়তে শিখেছে। তারপর তারা পা বাড়িয়েছে নক্ষত্রের পানে। এই লেখায় মানুষের মহাকাশ অভিযাত্রারই ইতিহাস তুলে ধরবো।
১/ আজ হতে প্রায় চারশ ছয় বছর আগে, ইতালির এক মধ্যবয়স্ক বিজ্ঞানী লম্বা আকৃতির কাচ বসানো এক অতি-আশ্চর্য যন্ত্র দিয়ে তাকালেন দূরের মিটিমিটি বিন্দুর মতো নক্ষত্রগুলোর দিকে। স্পষ্ট দেখলেন ওগুলো আসলে মোটেই আলোর বিন্দু নয়, বরং বিশাল আকারের জ্বলন্ত গোলক। কোন কোন নক্ষত্র মিটিমিটি জ্বলতো না। যন্ত্র দিয়ে তাকিয়ে দেখা গেল, সেগুলো আসলেই নক্ষত্র নয়, বরং পৃথিবীর মতোই গ্রহ।
এই বিজ্ঞানীর নাম গ্যালিলেও গ্যালিলি। যন্ত্রটার নাম টেলিস্কোপ, যা দিয়ে রাতের আকাশে তাকিয়ে তিনি দেখেন বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলোকে, আরো দেখেন চাঁদের গায়ের কলঙ্ক আসলে অতিকায় গর্ত, আর দেখেন শুক্র গ্রহের দশা (phase) পরিবর্তন।
আজ পেছন ফিরে তাকালে অবাক লাগে, সেদিনের সেই ছোট্ট লাঠির মতো যন্ত্রটির সাহায্যে চল্লিশোর্ধ্ব বিজ্ঞানীটি মহাকাশ গবেষণার দুয়ার খুলে দিলেন! গ্রহ-নক্ষত্র চলে এলো আমাদের হাতের মুঠোয় (বা চোখের নিকটে!)।
২
টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পরে গ্রহ-নক্ষত্র তো দেখা গেল, কিন্তু এরা কেনই বা ঘোরে, আর কেনই বা ছোটাছুটি করে ধুমধাম একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়ে না, সেই রহস্যের সমাধান গ্যালিলেও করে যেতে পারেন নি। পারবেনই বা কীভাবে আবিষ্কার করে যা জেনেছেন, সেটা জনসমক্ষে বলতেই তো সবাই ক্ষেপে গেল! ভাবখানা এমন, যেন গ্যালিলেও নিজের হাতে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরাচ্ছেন। এত বড় আস্পর্ধা!
যাই হোক গ্যালিলেওর মৃত্যুর বছর (১৬৪২) জন্ম নিলেন এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, নাম আইজ্যাক নিউটন। নিউটন ছিলেন যাকে বলে ‘বস পাবলিক’! কত বড় বস জানেন? এই লোক একটা বই লিখেছিলেন, যে বইয়ে তিনি গতির তিন বিখ্যাত সূত্র, মহাকর্ষ বলের বিখ্যাত সূত্র, এবং কেপলারের গ্রহঘূর্ণনের সূত্রের প্রতিপাদন (derivation) লিখে ফেললেন। একটু থেমে জাস্ট ব্যাপারটা চিন্তা করেন, এই তিনটা জিনিস আলাদা আলাদা বইয়ে লিখলেও সেটা যুগান্তকারী ব্যাপার হতো।
কিন্তু নিউটনের কাছে এগুলা যেন কোন “বিষয়ই নাহ!”, তাই তিনি গড়গড় করে তিনটাকেই এই বইতে এঁটে দিলেন। বইটার নাম “ফিলসফে ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা” (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, তাদের সকলের জন্য অবশ্যপাঠ্য। সূত্র শেখার জন্য না, সেসব তো যে কোন বইতেই পাওয়া যায়। নিউটনের চিন্তাভাবনাকে বুঝার জন্য।
৩/ নিউটনের এই আবিষ্কারগুলোর হাত ধরে গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব একেবারেই সহজ হয়ে উঠলো। ততদিনে মোটামুটি সবাই (অন্তত বিজ্ঞানের ছাত্র আর যাদের ঘটে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে) মেনে নিয়েছে যে গ্যালিলেও গ্যালিলি আসলে ঠিকই বলছিলেন। নিউটনের সূত্র কাগজে কলমে যা প্রমাণ করছে, গ্যালিলেওর টেলিস্কোপে তাকিয়ে বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে!
দেখা তো হলো, এবার মানুষের মনে ইচ্ছা জাগলো, এইসব দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে যাওয়া যায় কেমনে ভাই? পৃথিবীর বুকে লাফায় তো আর বেশিদূর ওঠা যাচ্ছে না। উপায় কী?
এই উপায়ের সন্ধান দিল নিউটনেরই আরেক দেশিভাই, উইলিয়াম মুর। নিউটনের বইটা বের হবার প্রায় ১২৬ বছর পরে ১৮১৩ সালে মুরসাহেব দিলেন রকেট থিওরি। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের (প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে) ওপর ভিত্তি করে এই ইংরেজ গণিতজ্ঞ রকেট বানানোর মশলা (সূত্র) বের করলেন। সহজ করে বললে, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাকাশে রওনা দিতে গেলে মাটির দিকে জোরে একটা ধাক্কা দিতে হবে। এই ধাক্কার সমান আর বিপরীত ধাক্কায় আমরা সাঁই করে আকাশের দিকে উঠে যাব! রকেট!
৪/ এখন হয়ত ভাবছেন, “তাইলে তো হইলোই। সূত্র যখন বানাইছে, রকেটটাও বানাই ফেলো ভাই! আকাশে উইড়া যাই!”
একটু ধৈর্য ধরেন। সূত্র বের করার পরে বাস্তবে সেটা দাঁড় করাতে একটু সময় লাগে। আমাদের লেগেছিল প্রায় দুইশ বছর। এর মাঝে কী কী বেরুলো সেটা একটু জেনে নেই বরং।
রকেট সূত্রের প্রায় ২৭ বছর পরে সর্বপ্রথম চাঁদের টেলিস্কোপিক ছবি তোলেন জন উইলিয়ান ড্রেপার। এই বিজ্ঞানী ভদ্রলোকও ব্রিটিশ-আমেরিকান। এতদিন কবি সাহিত্যিকরা যে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনার রঙে গল্পকথা সৃষ্টি করেছেন, সেই চাঁদ দ্বিমাত্রিক কাগজে ছবি হয়ে চোখের সামনে হাতের মুঠোয়! যদিও সে ছবি ছিল সাদা-কালো, তবুও তা কম কী!
কবি সাহিত্যিকদের কথা যখন এলোই, তখন দুয়েকটা সাই-ফাই বা বৈজ্ঞানিক কল্পগল্পের কথা না বললেই না। মহাকাশ নিয়ে গবেষণার এই শিশুকালে সাহিত্যিকরা মনের মাধুরী মিশিয়ে একের পর এক লিখেছেন নানারকম কাহিনী। ভবিষ্যতের কাহিনী। বিজ্ঞানের জয়-জয়কারের কাহিনী। মহাকাশযাত্রার বিচিত্র অভিযানের গল্প! জুলভার্ন এই সময়েরই (১৮২৮-১৯০৫) লেখক।
চাঁদের ছবি দেখেই কি না কে জানে, ১৮৪০ সালে তিনি লিখলেন “ফ্রম দ্যা আর্থ টু দ্যা মুন” উপন্যাস। আশ্চর্যজনকভাবে, এই সাই-ফাই উপন্যাসে চন্দ্রযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, যা অনেকটাই পরবর্তীতে মিলে গেছে। হিসাব-নিকাশও করেছিলেন, যদিও তা ঠিক বাস্তবিক হয় নাই। তবুও, এই বা কম কী! সাহিত্যিকরা বিজ্ঞানের কাছাকাছি থাকলে এক চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয় কিন্তু!
আরেকটা উপন্যাসের কথা না বললেই নয়। এইচ.জি. ওয়েলসের “দ্যা ওয়ার অফ দ্যা ওয়ার্ল্ডস”। বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে (১৮৯৮) প্রকাশিত উপন্যাস পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমেরিকান এক পদার্থবিজ্ঞানী, রবার্ট হাচিংস গদার। এলিয়েন বা ভিন্ গ্রহের প্রাণীরা যদি পৃথিবীতে এসে আক্রমণ করেই বসে, তাহলে আমরা কীভাবে লড়াই করবো? বাঁচবোই বা কীভাবে? বলা হয়, এই গল্পের অনুপ্রেরণাতেই রবার্ট গদার তরল জ্বালানির রকেটের উদ্ভাবনের প্রথম ধাপগুলো বের করেছিলেন!
৫/ যাক, এতোক্ষণে কিছু কাজের আলাপ শুরু হচ্ছে – এটাই ভাবছেন নিশ্চয়ই! রবার্টসাহেবের হাত ধরেই আধুনিক রকেটের প্রথম মডেলগুলো বের হয়েছিল। চাঁদের দিকে যাত্রা তবে শুরু! নাহ। আবারও একটু ধৈর্য ধরতে বলবো। এত সহজ ছিল না আমাদের যাত্রা। ১৯২৬ থেকে ১৯৪১ সালের মাঝে গদারের বিজ্ঞানীর দল মোট ৩৪টি রকেট সফলভাবে চালু করতে সক্ষম হন। এই রকেটগুলোর অতিক্রম করা সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ২.৬ কিলোমিটার, আর সর্বোচ্চ গতি ছিল ৮৮৫ কিমি/ঘন্টা।
বুঝতেই পারছেন, এই গতি দিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া হয় নি। তবে অগ্রগতির গ্রাফ ক্রমেই উর্ধ্বগামীই হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই ‘সাফল্য’গুলো মাত্র ১৫ বছরের গবেষণা এবং “অ্যাপ্লিকেশনের” ফলাফল। এটাও কম না একেবারে!
এখানে একটা ছোট কথা বলে রাখতে চাই। আমাদের অনেকের কাছেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে একটা রোমান্টিকতা কাজ করে। গবেষণার কথা বললেই চোখে ভাসে মুভিতে দেখা কোন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ঝড়ের বেগে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলছেন এমন কোন সিকোয়েন্স। পেছনে হয়তো বাজতে থাকে দারুন আশা-জাগানো আবহ সঙ্গীত। বাস্তবে গবেষণার পেছনে অত্যন্ত একঘেঁয়ে এবং কষ্টকর শ্রম জড়িয়ে থাকে। রাতের পর রাত জেগে কঠিন কঠিন ধাঁধার সমাধান বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।
একটা সফল রকেট বানাতে অজস্র খুঁটিনাটি সূত্র আর বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে হয়। পদার্থগুলোর অবস্থা জানতে হয়, গতিবিদ্যা জানতে হয়, যন্ত্রপাতির গঠন জানতে হয়, মেকানিক্স নামক জটিল বিদ্যা গুলে খেতে হয়। অনেকজন মিলে কাজ করতে হয়, যেখানে বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়েও ঠুকাঠুকি লেগে যেতে পারে। কোন পন্থায় এগুলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, সেটা যখন কেউই জানে না, তখন অনুমান বা কিছুটা যুক্তি-তথ্যের ভিত্তিতে “এজুকেটেড গেস” (শিক্ষিত অনুমান?) করতে হয়। সেই পন্থা ফেল করলে আরেক রাস্তা।
তারপর আরেক রাস্তা। ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। অনেকেই হাল ছেড়ে দেন। টাকাপয়সা যারা দেয়, সেসব ‘গৌরী সেন’রাও হতাশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। এতসব বাধা পেরিয়েই তবে একেকটা সফলতা আসে। তাই আপনি যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেই সিনেম্যাটিক রোমান্টিক আইডিয়া নিয়ে বসে থাকেন, সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এ বড় বন্ধুর পথ। পদে পদে বাধা আর হতাশা। তবে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরাই যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসেন। ভাবেন তো একবার, এমন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সাফল্য এলে কী অপার্থিব আনন্দ হয়? এই আবিষ্কারের নেশা তাই আমাদের জ্বালানি।
৬/ রবার্ট গদারের রকেট আবিষ্কারের এই সময়টায় বাকি বিশ্বের প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোও বসে ছিল না। এসময়ে ইউরোপের অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ডসহ সোভিয়েত রাশিয়াতে রকেট বিজ্ঞানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। সময়টা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল, যে সময়ে এই দেশগুলো প্রত্যেকেই আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ১৯২৬ সালে গদারের তরল জ্বালানির প্রথম রকেট আবিষ্কারের তিন বছর পরেই জার্মানিতে হারম্যান ওবার্থের নেতৃত্বে তরল জ্বালানির প্রথম রকেট তৈরি হয়।
বছর দুয়েক পর জার্মানির সামরিক বাহিনী রকেটের ইঞ্জিন বানাতে সক্ষম হয়। সোভিয়েত রাশিয়াও পিছিয়ে ছিল না। ১৯৩৩ সালে তাদের প্রথম তরল জ্বালানির রকেট তৈরি হয় সার্গেই কোরোলভের নেতৃত্বে। ১৯৩৩ সালেই নাৎজি জার্মানিতে তৈরি হয় “অ্যাগ্রেগেট সিরিজের” প্রথম রকেট। এইগুলো থেকেই পরবর্তীতে ভি-২ সিরিজের ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করেছিল তারা। ভি-২ সিরিজের মিসাইলগুলো সর্বপ্রথম কারমান রেখা (Kármán line, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০০ কিমি উপরের একটি কাল্পনিক রেখা, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশের সীমানা রেখা) পার করতে সক্ষম হয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঁধে গেছে।
বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র এই ভি-২ সিরিজের চেয়ে উন্নত রকেট বানাতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪ অক্টোবরে তাদের ওড়ানো রকেট থেকে ভূপৃষ্ঠের প্রথম ছবি তোলা হয়। বলতে হচ্ছে যে, প্রায় ৪০ হাজার বর্গমাইলের এই ছবিটাই পৃথিবীর প্রথম সেলফি! হা হা হা!
এর মাত্র চার মাস পরই তারা রকেটে করে সর্বপ্রথম প্রাণীকে মহাকাশে পাঠায়। প্রাণী শুনেই খুব উৎসাহী হচ্ছেন, কোন প্রাণী সেটা শুনে উৎসাহ একটু নিভে যেতে পারে। পৃথিবী থেকে রকেটে করে পাঠানো প্রথম প্রাণী হলো এক প্রকার মাছি (fruit fly)!
৭/ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের গতিকে অনেকটা এক্সপোনেনশিয়াল রেখার সাথে তুলনা করা যায়। এতক্ষণ যে প্রগতির কথা বললাম, তা ঘটেছে অনেক ধীর গতিতে। মাঝের অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বা “ব্রেক-থ্রু” ছাড়াই। কিন্তু যতই সময় গিয়েছে, বছরগুলোর দূরত্ব ক্রমেই কমে এসেছে। মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে সেই গ্যালিলেও থেকে ১৯৫৭ সালের আগের পুরো সময়টাকে একটা ভাগে রাখা হয়। আর এর পরে প্রতি দশককে আলাদা আলাদা ভাগে রাখতে হয়।
কারণ এ সময়ে প্রতি দশ বছরেই প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের গতি এত বেশি ছিল, যে প্রতি দশককে আলাদা ধাপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। ১৯৫৭ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙনের আগে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মহাকাশ যাত্রার ‘শীতল’ প্রতিযোগিতাকে ‘স্পেস রেস’ বলা হয়। ১৯৫৭-এর বিশেষত্ব কী? এই বছর রাশিয়া সফলভাবে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করে। এর নাম ছিল স্পুটনিক-১। এক মাস পরেই তারা বিখ্যাত স্পুটনিক-২ এর যাত্রা হলো, যে উপগ্রহের যাত্রী ছিল লাইকা নামের একটি কুকুর।
দৌড়ে একটু দেরি করে ফেললো যুক্তরাষ্ট্র, তবু দুইমাস পরই তারা তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১-কে মহাকাশে পাঠালো।
কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর দৌড়ে রাশিয়া জিতে যাওয়ার পরের ধাপ হলো চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর দৌড়। এই দৌড়েও রাশিয়াই জিতলো। ১৯৫৯ সালে তাদের পাঠানো লুনা-১, লুনা-২ এবং লুনা-৩ তিনটাই সফল যাত্রা ছিল। লুনা-৩ তো চাঁদের যে পিঠটাকে আমরা কখনই দেখতে পারি না সেই পৃষ্ঠের ছবি তুলেও পাঠালো!
৮/ ষাটের দশকের (১৯৬০-১৯৬৯) পুরোটাই ছিল এই দুই দেশের মধ্যে কে কার আগে কী পাঠাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা। রাশিয়া গাছপালা পাঠায়, তো আমেরিকা শিম্পাঞ্জি পাঠায়। এই না দেখে রাশিয়া একজন আস্ত মানুষই পাঠিয়ে দিল! ভদ্রলোকের নাম য়ুরি গ্যাগারিন। ভোস্টক-১ যানে করে ১৯৬১ সালে তিনি মহাকাশ দাপিয়ে এলেন। আমেরিকাও অ্যালান শেপার্ড নামের এক মহাকাশচারীকে পাঠালো একই বছর ফ্রিডম-৭ যানে করে।
এরপর রাশিয়া আরেকটু এগিয়ে শুক্র গ্রহের কাছে যান পাঠালো। অন্যদিকে আমেরিকা বানালো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা মানমন্দির ও.এস.ও-১। রাশিয়া ভাবলো খালি পুরুষরাই যাবে কেন? রাশিয়ান নারীরাও কম যায় না! মহাকাশে উড়লেন ভ্যালেন্তিনা তারাশকোভা।
এরই মাঝে কেটে গেছে প্রায় পাঁচ বছর। ১৯৬৫ সাল। রাশিয়ার অ্যালেক্সেই লেওনভ মহাশূন্যে যান থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে নিলেন। অন্যদিকে আমেরিকা মেরিনার-৪ পাঠিয়ে দিল মঙ্গল গ্রহের পাশ দিয়ে। যাবার সময় মঙ্গলের মঙ্গলময় ছবি তুলে ফেললো সে। এই প্রথম আমেরিকান একটা মহাকাশযান এমন কিছু করে দেখালো যেটা রাশিয়ান কোন মহাকাশযান করে দেখায় নি।
হাড্ডাহাড্ডি এই লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য দাঁড়িয়ে গেল – কে সবার আগে চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারে। শুরুতে বারবার পিছিয়ে পড়া আমেরিকাই শেষ হাসি হাসলো, ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই চাঁদের বুকে পা রাখলেন অ্যাপোলো-১১ যানের নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন।
৯/ সত্তুরের দশকের পুরোটাই ছিল একইরকমের লড়াই। কে কার আগে কোথায় পৌঁছুতে পারে। চাঁদ ‘বিজয়ের’ পরে সবার চেষ্টা শুরু হলো সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলোতে মহাকাশযান পাঠানোর। বিস্তারিত তথ্যগুলো দিয়ে লেখাটাকে অযথাই লম্বা না করি। আগ্রহীগণ ইন্টারনেটে একটু ঘাঁটলেই জানতে পারবেন। এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট ছিল আমেরিকার আন্তনক্ষত্রীয় মহাকাশযান ভয়েজার-১ এবং ভয়েজার-২ এর যাত্রা। ১৯৭৭ সালে যাত্রা করে এই দুইটি মহাকাশযান সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। যাবার পথে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে আমাদের কাছে। আমরাও আমাদের দৃষ্টিসীমার বহু বাইরের গ্রহ-নক্ষত্রকে নতুন চোখে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করছি!
ভয়েজার সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহেরই ছবি তুলে আমাদের পাঠিয়েছে। এই দশকেই সোভিয়েত রাশিয়া ধীরে ধীরে ‘স্পেস রেসে’ পিছিয়ে পড়তে থাকে। নিত্যনতুন যাত্রা বা আবিষ্কারে যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে টেক্কা দিতে শুরু করে। যদিও আশির দশকে ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার অন্যতম অনবদ্য প্রোজেক্ট ছিল প্রথম মহাকাশ স্টেশন ‘মির’ গড়ে তোলা।
১৯৯১ এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়লো। ‘স্পেস রেস’ও থেমে গেল। নব্বুইয়ের দশক থেকে বিভিন্ন দেশ একত্রে মিলে প্রোজেক্টগুলো শুরু করলো। একটি কারণ স্পেস রেস না থাকা। আরেকটি কারণ এতদিনে মহাকাশ যাত্রার খরচ ও জটিলতা এমন পর্যায়ে গেছে যে একাধিক গুণী মাথা একজায়গায় না হলে তা দ্রুত সঠিক উপায়ে সমাধান করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নাসা’র সাথে যুক্তরাজ্যের সার্ক, নেদারল্যান্ডসের নিভ্র, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি, জাপানের আইসাস, কানাডা, ইতালি, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ বিভিন্ন সময়ে একযোগে মহাকাশের নিত্যনতুন যাত্রাকে সফল করে তুলেছে। নব্বুইয়ের শেষভাগে শুরু হয়েছিল মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান অবতরণের প্রোজেক্টগুলো। পাথফাইন্ডারের কথা কার কার মনে আছে? এর পরপরই ১৯৯৮ সালে তৈরি করা হয়েছে বহুজাতিক মহাকাশ স্টেশন আই.এস.এস।
১০/ শুরু হলো একবিংশ শতাব্দী। গত ১৭ বছরে মহাকাশযাত্রা পৌঁছে গেছে অনেক অনেক উচ্চতায়। চারশ বছর আগে গ্যালিলেও বানিয়েছিলেন টেলিস্কোপ। চারশ বছর পরে নাসা বানালো মহাজাগতিক টেলিস্কোপ, বানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল মহাশূন্যে। এই টেলিস্কোপের কাজ হবে মহাকাশের বিপুল নক্ষত্ররাজি আর তার গ্রহমালা ঘেঁটে পৃথিবীর মতই অন্য গ্রহগুলোর খোঁজ দেয়া।
প্রোজেক্টের নাম – কেপলার মিশন! এই তো, গতবছরই এই টেলিস্কোপে ধরা পড়লো বহুদূরের দু’টি “এক্সোপ্ল্যানেট”, যা পৃথিবীর মতোই কোন নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে এবং সঠিক দূরত্বের সীমার ভেতরে থাকার কারণে এই গ্রহগুলোতে প্রাণের বিস্তার অধিকতর সহজ হবে। বলা যায় না, কেপলার মিশনের খুঁজে পাওয়া কোন এক গ্রহই হয়তো হবে আমাদের পরবর্তী ভিটেমাটি!
বছর চারেক আগে ভয়েজার সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেল অনেক দূরে। ২০১৪ সালে ঘটলো আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির একটি প্রোজেক্টের আওতায় ধূমকেতুর ওপরে একটা প্রোব সফলভাবে বসিয়ে দেয়া হলো। প্রজেক্টের নাম ছিল রোসেটা।
২০০৬ সালে যাত্রা করা নিউ হরাইজনস মহাকাশযানটির কাজও ভয়েজারের মতোন। এই প্রোবটিই বছরখানেক আগে (জুলাই ২০১৫) প্লুটোকে পার হয়ে গিয়েছে। পার হবার সময় ফটাফট কতগুলো ছবিও তুলে নিয়েছে।
অবশেষে বলা যায় যে, আমার মতে, মানুষের সম্মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশ বিবর্ধমান। এজন্য আশা হারানোর বা হাল ছেড়ে দেয়ার কোন কারণই নেই। বিজ্ঞানের যাত্রা কারো একার দায়িত্ব নয়। এই দায়িত্ব সবার। এই পথের আনন্দও সবার। মহাকাশ যাত্রার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। শুরুর দিকে একেকটা যুগ এসেছে যখন দীর্ঘ সময় ধরে কোনকিছুই তেমন আবিষ্কার হয় নি।
কিন্তু একবার যখন শুরু হয়েছে, তখন তা আর থামে নি। নিজে নিজেই আবিষ্কারের গতি বেড়েছে। চিন্তা করে দেখুন তো, ইদানিং যেরকম অহরহই নতুন আবিষ্কারের খবর পাচ্ছেন, তা কি আগে আদৌ কেউ ভেবেছিল? এর কারণ আমাদের সম্মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। এর ধাপে দাঁড়িয়েই আমরা পরবর্তী আবিষ্কারের দিকে হাত বাড়াই, বাড়ানোর সাহস হয়। আইজ্যাক নিউটনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, “If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.”
মহাকাশ যাত্রার এই মহাযজ্ঞ দেখলে নিউটনের উক্তিটার মর্মার্থ ধরা পড়ে!
ঢাকা, ১৪ অক্টোবর, (ক্যাম্পাসলাইভ২৪.কম)// আইএইচ
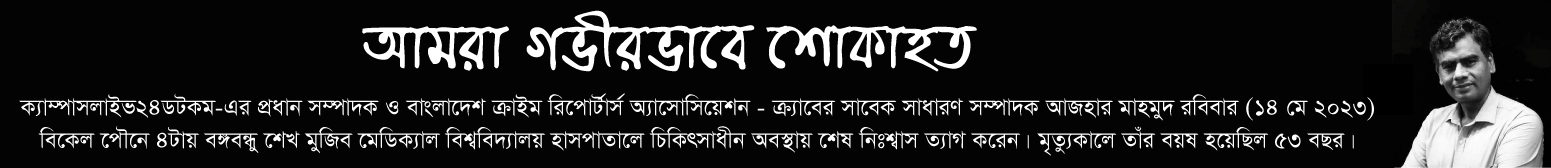
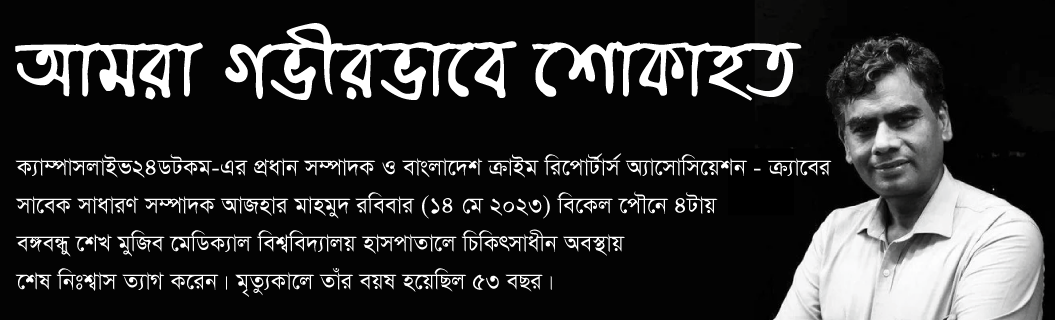



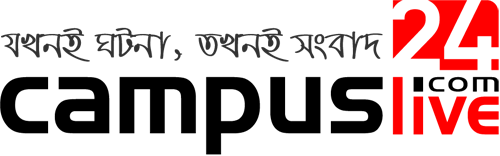
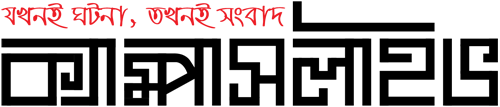















আপনার মূল্যবান মতামত দিন: